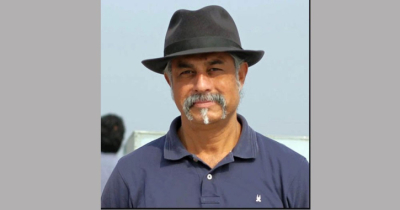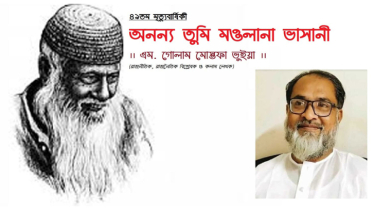রাজনীতি গিলে ফেললো দৈনিকের মাস্টহেড!
প্রকাশ: ১৯:৫৯, ১৯ নভেম্বর ২০২৫

বাসা খুঁজতে গিয়ে এক চিকিৎসক ও গবেষকের সঙ্গে পরিচয়, দীর্ঘ আলাপ। দেশের শীর্ষ ক’জন সাংবাদিকের বন্ধুও তিনি। ঘণ্টা দু’য়েকের আড্ডায় বললেন, রাজনীতি ছাড়া গণমাধ্যমের আর কোনো এজেন্ডা দেখি না। দেশে কত কত সমস্যা, সেগুলো নিয়ে অনুসন্ধান নেই। পত্রিকার পাতাজুড়ে শুধুই রাজনীতির খবর। শেষে বললেন, আজকের অপরাজনীতির জন্য গণমাধ্যমই দায়ী। জানালেন, জীর্ণ-শীর্ণ-গরিব এক নারী সাংবাদিক এখানে ভাড়া থাকতেন। কয়েক বছরেই তার অস্বাভাবিক বদল দেখে তিনি বিস্মিত। এখন শুনছেন, ব্যাংকে তার কোটি কোটি টাকা!
মন-খারাপ নিয়ে বাসায় ফিরলাম। ফেসবুকে ঢুকে দেখলাম, ‘শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের’ খবরের জন্য ‘প্রতিদিনের বাংলাদেশ’-এর মাস্টহেড ফুটনোটে নামিয়ে ফেলার ঘটনা নিয়ে সবাই কৌতূহলী। গণমাধ্যমের বিরল এই ঘটনাকে অনেকেই স্বাগত জানাচ্ছেন। কেউ কেউ আবার অস্বাভাবিক বলছেন। কৌতূহলবশত পত্রিকাটিতে কর্মরত আমার সাবেক সহকর্মীকে ফোন দিলাম। তিনি বললেন, খবরটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেই এমনটা করা হয়েছে।
সাংবাদিকতায় আমার গভীর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। তাই চ্যাটজিপিটির সঙ্গে আলাপে বসলাম। সে সাংবাদিকতা তত্ত্ব, সংবাদ-ডিজাইন দর্শন, রাজনৈতিক যোগাযোগ, সংবাদ-প্রতীকবাদের ভিত্তিতে বিস্তারিত তুলে ধরে জানাল, ঘটনাটি বিশ্বব্যাপী প্রিন্ট জার্নালিজমে খুবই বিরল। যা প্রেস ডিজাইনে আনপ্রেসিডেন্টেড। অর্থাৎ পত্রিকাটি বলতে চেয়েছে খবরটি তাদের সবচেয়ে কোর ব্র্যান্ডিং অংশ বা মাস্টহেডের চেয়েও বড়। অনেকগুলো দৃষ্টান্ত তুলে ধরে জানাল, মাস্টহেডের রঙ বদল, ডানে-বামে সরানো, ফ্রন্টপেইজ খালি রাখার মতো ঘটনা থাকলেও মাস্টহেড নিচে নামানো সত্যিই বিরল।
রাজনীতির রূপকথাভিত্তিক গল্পের মহামারিতে আক্রান্ত পত্রিকাগুলো যেখানে নেতাদের খবরের চাপে স্পেশাল, এক্সক্লুসিভ নিউজও সরিয়ে দেয় সেখানে মাস্টহেড পায়ে পিষে ফেলা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসন পর্যন্ত এ ভূখণ্ডের মানুষের দীর্ঘ লড়াইয়ের জিন ভীষণ সক্রিয়। গণমাধ্যমগুলো একুশ শতকের তৃতীয় দশকে এসেও সেই জিনের আসরে রাজনৈতিক নেতাদের ‘মহামানব’ হিসেবে দেখাতে গিয়ে ‘দানবে’ পরিণত করছে প্রতিনিয়ত।
দেশীয় গণমাধ্যমের এমন প্রবণতার উৎস জ্ঞান বিবর্তনভিত্তিক হাইপার-এজেন্সি ডিটেকশন থিওরিতে পাওয়া যায়। যেখানে বলা হয়েছে, মানুষের মস্তিষ্ক বিবর্তনের পথে ‘ইচ্ছাকৃত শক্তি বা এজেন্ট’ খোঁজার প্রবণতা তৈরি করেছে। আবার কস্টলি সিগনালিং থিওরি মতে, কোনো নেতা যখন ত্যাগ, দুঃসাহস বা নৈতিকতার চরমতম দিক প্রদর্শন করেন, মানুষ তাকে অসাধারণ ধরে নিয়ে দেবতার মতো মর্যাদা দেয়। এসব থিওরির মূল কথা হচ্ছে, মানুষ যখন নিজেকে দুর্বল অনুভব করে তখন শক্তিশালী নেতা–দেবতার দিকে ঝোঁকে।
তাহলে প্রশ্ন, গণমাধ্যম কি জনগণকে শক্তিমুখী করার বদলে দুর্বল করে তোলে? ন্যারেটিভ লজিক মতে, খবর হচ্ছে সেই গল্প যা হিরো, ভিলেন, সংকট, উদ্ধারের ঘটনায় মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত, দুর্বল, বঞ্চিত চরিত্রে দেখায়। ডিপেনডেন্সি থিওরিতে বলা হয়, মানুষ যখন সমস্যার সমাধান জানে না, সব তথ্য মিডিয়া থেকে নেয়, তখন তাদের নির্ভরশীলতা বাড়ে। গণমাধ্যম তখন মানুষের দুর্বলতার অনুভূতি উৎপাদন করে।
মোরাল প্যানিক থিওরি মতে, গণমাধ্যম যখন অপরাধ, সংকট, বিশৃঙ্খলা, হুমকিকে অতিরঞ্জিতভাবে দেখায়, তখন মানুষের মধ্যে ‘আমরা অসহায়’ অনুভূতি তৈরি হয়। তাছাড়া কাল্টিভেশন থিওরি বলছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ব্রেকিং নিউজ, টকশো দর্শকদের মধ্যে ধারণাগত দুর্বলতা তৈরি করে। তারা ভাবতে থাকে, ‘সমাজ আরও বিপজ্জনক’, ‘আমি ছোট, ক্ষমতাহীন’।
মিডিয়া লিটারেসি যেখানে জোরালো নয়, মাস্টহেড পায়ে দলিয়ে কোনো ঘটনাকে নিজেদের অস্তিত্ব বা পরিচয়ের চেয়েও বড় দেখিয়ে খুব বেশি লাভ হবে কি? আমি ঠিক জানি না। তবে আমার মনে হয়, বর্তমান প্রজন্ম গণমাধ্যমের এসব চমকে-ধমকে খুব বেশি আগ্রহী নয়। তারা জানতে চায়, নেতা যত বড়ই হোক, তিনি জবাবদিহিতার জন্য কতটা দায়বদ্ধ। দল যত বড়ই হোক নিজেরা গণতন্ত্র চর্চা করে কিনা। আদর্শ যত বড়ই হোক, দলের চেয়ে দেশ অগ্রাধিকার পাচ্ছে কিনা। আর সবশেষে তারা বলতে চায়, গণমাধ্যম যত বড় আর প্রভাবশালীই হোক না কেন, দলমত নির্বিশেষে মানচিত্রের ভেতরে সব মানুষের অধিকারের পক্ষে কিনা, সেটাই নিশ্চিত করা জরুরি।
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক