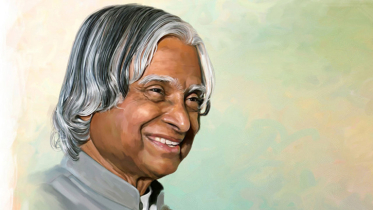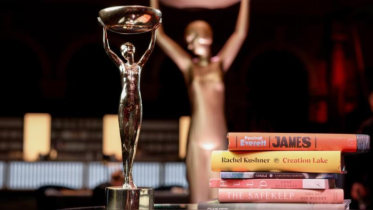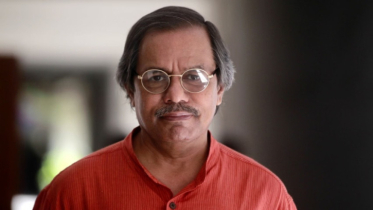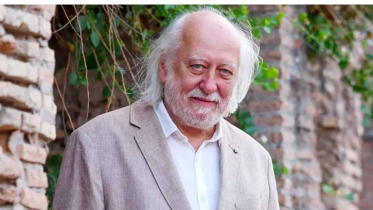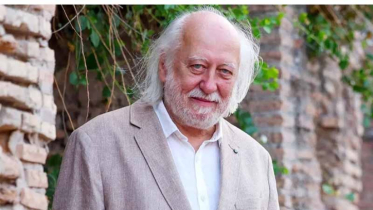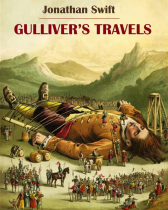বিশ্ব সাহিত্যের ধ্রূপদি রচনা
তিন শতাব্দী পরও প্রাসঙ্গিক ‘গালিভারস ট্রাবেলস’
মাইসারা জান্নাত
প্রকাশ: ০৯:৪২, ২৮ অক্টোবর ২০২৫ | আপডেট: ১২:৫৮, ২৮ অক্টোবর ২০২৫
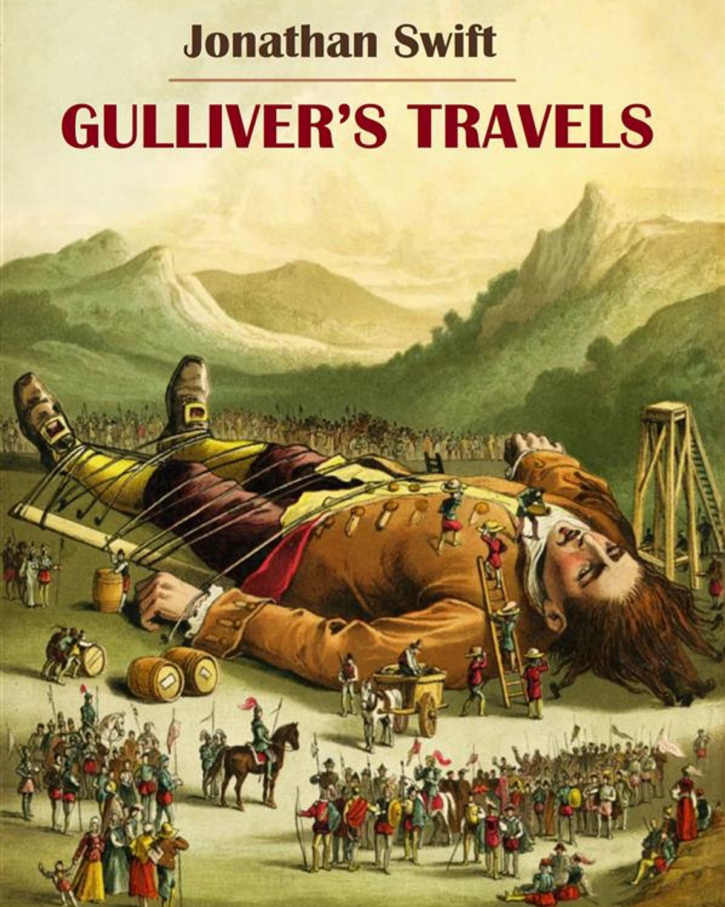
১৭২৬ সালের ২৮ অক্টোবর লন্ডনে প্রকাশিত হয় বিশ্ব সাহিত্যের ধ্রূপদি গল্প গালিভারস ট্রাবেলস। লেখক জোনাথন সুইফট। তিনি ছিলেন আয়রিশ পুরোহিত, লেখক ও ব্যঙ্গরচয়িতা। তৎকালীন ইউরোপ ছিল যুদ্ধ, দাসপ্রথা ও বৈষম্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানুষ সভ্যতার দাবিদার হলেও ভেতরে ছিল অসভ্যতা। সেই সময়ে সুইফট এই বই লিখেছেন, যেখানে ভ্রমণ কাহিনির মোড়কে তিনি মানবসমাজের দ্বিচারিতা, স্বার্থপরতা ও ভণ্ডামিকে তুলে ধরেছেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক রচনায়।
প্রথম প্রকাশের পর থেকেই বইটি সাহিত্যপ্রেমী ও সাধারণ পাঠকের মধ্যে আলোচনার ঝড় তোলে। অনেকেই একে শিশুতোষ গল্প ভেবে পড়তে শুরু করেন, কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরই বোঝা যায়, এটি একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গরচনা, যেখানে মানুষের সমাজ, রাজনীতি, বিজ্ঞান, নৈতিকতাসহ সবকিছুকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করা হয়েছে।
এই গল্প অবলম্বনে বহু নাটক সিনেমা তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় অনূদিত হয়েছে বইটি। তৎকালীন সুইফটকে লেখা এক চিঠিতে জনগে নামক একজন জানিয়েছিলেন, ‘ক্যাবিনেট কাউন্সিল থেকে নার্সারি, সর্বত্রই এই বই পঠিত হয়।’ এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল বইটি। আজও জনপ্রিয়তার তুঙ্গে।
জোনাথন সুইফটের জীবনও ছিল তার লেখার মতোই সংগ্রামী। তিনি ১৬৬৭ সালে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। লেখালেখির শুরু থেকেই তিনি রাজনীতি ও ধর্মীয় কপটতার বিরুদ্ধে কলম ধরেন। অ্যা মডেস্ট প্রপোজাল এবং দ্য ব্যাটল অব দ্য বুকসের মতো রচনায় তিনি যেমন সামাজিক অব্যবস্থাপনার ব্যঙ্গ করেছেন, তেমনি গালিভারস ট্রাবেলসে মানবসভ্যতার অন্তর্গত রোগগুলো তুলে ধরেছেন গভীর শিল্পবোধে। সুইফট ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে প্রখর ব্যঙ্গরচয়িতাদের একজন, যিনি মজার গল্প বলার ছলে পাঠককে নিজের ভেতরের মানুষটাকে চিনাতে বাধ্য করেছেন।
গালিভারস ট্রাবেলস গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লেমুয়েল গালিভার, যিনি পেশায় একজন চিকিৎসক। একদা সমুদ্রযাত্রায় বের হন। চারটি দেশে যান। প্রতিটি যাত্রায় তিনি ভিন্ন ভিন্ন অদ্ভুত দেশে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন।
এই চারটি ভ্রমণ কাহিনির মাধ্যমে লেখক মানুষের সভ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। মানুষের ভেতরের স্বার্থ, হিংসা ও অহংকারকে ব্যঙ্গাত্মক রূপে চিত্রায়িত করেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণী উল্লেখ করা হলো।
লিলিপুট
গালিভার প্রথমে পৌঁছান লিলিপুটে। ঝড়ের কবলে পড়ে তার জাহাজ ডুবে যায়। বহুকষ্টে তীরে পৌঁছান তিনি। চোখ মেলে দেখেন স্বাভাবিক কোনো জায়গা নয়, বরং এটা লিলিপুটদের রাজ্য। মাত্র ছয় ইঞ্চির বামন মানুষরা গালিভারকে বন্দী করেন। পরে বুদ্ধি খাটিয়ে সেখান থেকে মুক্ত হন তিনি।
ক্ষুদ্র এই জাতির রাজনীতি ও সমাজ দেখে গালিভার বিস্মিত হন। তাদের রাজা ও মন্ত্রীদের মধ্যে চলতে থাকে অহেতুক ক্ষমতার লড়াই, কূটনীতি ও ষড়যন্ত্র। সেখানে শাসক নির্বাচন হয় দড়ির ওপর হাঁটার দক্ষতার মাধ্যমে। এ এক অদ্ভুত প্রতীক, যেখানে যোগ্যতার চেয়ে চাটুকারিতা ও কৌশলই সাফল্যের মাপকাঠি।
লিলিপুটের মানুষরা ছোট হলেও তাদের অহংকার অনেক বেশি। তারা নিজেদের জাতিকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, শত্রুদের ঘৃণা করে এবং অতি ক্ষুদ্র কারণেও যুদ্ধ শুরু করে।
ব্রবডিংনেগ
দ্বিতীয় ভ্রমণে গালিভার পৌঁছান ব্রবডিংনেগে। এদেশে মানুষ দৈত্যাকৃতির। তাদের মাঝে সে ক্ষুদ্র এক প্রাণী। এক দৈত্যরাজা গালিভারের কাছ থেকে ইউরোপের রাজনীতি ও সমাজ সম্পর্কে শুনে বিস্মিত হন। তিনি বলেন, মানুষ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক জীব, কারণ সে জ্ঞান ও শক্তি ব্যবহার করে ধ্বংস সাধন করে। এই বক্তব্যে সুইফট মানবসভ্যতার নৈতিক দেউলিয়াত্বকে প্রকাশ করেছেন।
ব্রবডিংনেগে মানুষ বৃহৎ হলেও তারা সরল ও নীতিবান। সেখানে নেই ষড়যন্ত্র, নেই ধনলোভ। বরং তারা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বেঁচে থাকেন। এই বিপরীত তুলনার মাধ্যমে সুইফট বোঝাতে চেয়েছেন, সভ্যতার মান নৈতিকতায়।
লাপুটা
তৃতীয় ভ্রমণে গালিভার যান লাপুটা নামের আকাশের ভাসমান দ্বীপে। এখানে সবাই বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও আবিষ্কারক। কিন্তু তাদের চিন্তা এতটাই বিমূর্ত যে, তারা বাস্তব জীবনের কোনো প্রয়োজনে মনোযোগ দিতে পারেন না। কেউ শসা থেকে সূর্যালোক বের করার চেষ্টা করেন, কেউ মাটির মাধ্যমে রক্ত তৈরি করতে চান। কিন্তু মানবতার প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে চিন্তা করেন না।
সুইফট এখানে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন তথাকথিত জ্ঞানীদের প্রতি, যারা বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের জগতে হারিয়ে যায়। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি কেবল কল্পনা, না মানুষের কল্যাণ? এই অংশ পড়লে আজকের প্রযুক্তিনির্ভর সমাজের চিত্রও মনে পড়ে, যেখানে মানুষ তথ্য ও যন্ত্রে ডুবে থেকে মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতা হারাচ্ছে।
হুইনহ্নিম ও ইয়াহু
শেষ ভ্রমণটি সবচেয়ে ব্যতিক্রম। গালিভার পৌঁছান এমন এক দেশে, যেখানে বুদ্ধিমান ঘোড়ারা সমাজ পরিচালনা করে। তাদের বলা হয় হুইনহ্নিম, আর মানুষসদৃশ বর্বর জীবদের বলা হয় ইয়াহু। হুইনহ্নিমরা যুক্তিবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও নীতিবান। তাদের সমাজে মিথ্যা, লোভ বা হিংসার কোনো স্থান নেই। কিন্তু ইয়াহুরা নোংরা, হিংস্র ও লোভী।
গালিভার এই সমাজে থেকে নিজের জাতিকে ঘৃণা করতে শেখে। সে উপলব্ধি করে, সভ্য মানুষ আসলে ইয়াহুর চেয়ে ভিন্ন নয়, বরং অনেক সময় তার চেয়ে বেশি কপট।
সুইফট এখানে মানুষের আত্মসমালোচনার এক গভীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, মানুষ তার অহংকারে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবলেও নৈতিকভাবে সে প্রায়ই নিচে নেমে যায়।
গালিভারের চারটি ভ্রমণ আসলে চারটি আয়না, যেখানে মানুষের রাজনীতি, বিজ্ঞান, সমাজ ও নৈতিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। সুইফট ভ্রমণকাহিনির মোড়কে এমন ব্যঙ্গরচনা তৈরি করেছেন, যা সময়ের সীমা পেরিয়ে আজও সমান প্রাসঙ্গিক।
আজকের পৃথিবীতেও আমরা দেখি ক্ষমতার লড়াই, নীতিহীন রাজনীতি, প্রযুক্তির মোহে হারিয়ে যাওয়া মানবতা। লিলিপুট, ব্রবডিংনেগ, লাপুটা ও হুইনহ্নিম, সব যেন আজও আমাদের চারপাশে। গালিভারের চোখে আমরা দেখি নিজেদের প্রতিচ্ছবি, কখনো ক্ষুদ্র, কখনো লোভী, কখনো অর্থহীন জ্ঞানপিপাসু হিসেবে।
তিন শতাব্দী পেরিয়ে আজও গালিভার আমাদের আহ্বান জানায়, নিজেকে বোঝো, নিজের সমাজকে দেখো এবং মানুষ হিসেবে মানবিক হও। তার ভ্রমণ শেষ হয়েছে, কিন্তু আমাদের সেই যাত্রা এখনো চলমান।