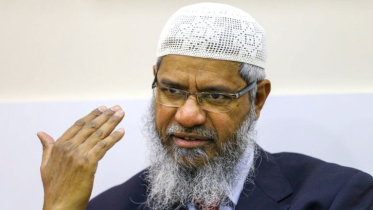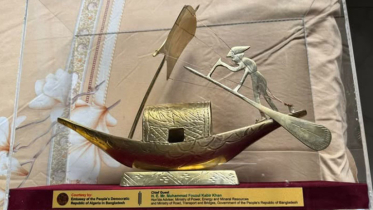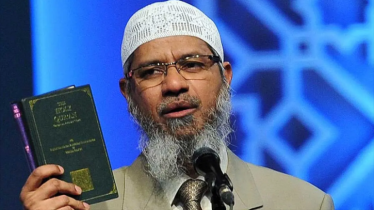৩৪ গিগাওয়াটের বেশি জীবাশ্ম বিদ্যুৎ সক্ষমতায় হুমকিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভবিষ্যৎ
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ: ১৪:২৪, ২৪ আগস্ট ২০২৫ | আপডেট: ১৫:৪৯, ২৪ আগস্ট ২০২৫

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বলছে, সরকারের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিকল্পনার অসামঞ্জস্যের কারণে একদিকে জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ সক্ষমতা ক্রমাগত বাড়ছে, অন্যদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়ছে।
নবায়নযোগ্য লক্ষ্য ও ঘাটতি
সিপিডির নতুন গবেষণায় দেখা যায়, ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সক্ষমতা দাঁড়াতে হবে ১৮,১৬২ মেগাওয়াটে। অথচ বর্তমান পরিকল্পনায় রয়েছে মাত্র ১,৯৬৭ মেগাওয়াট—যা আগামী পাঁচ বছরে ১৬,০০০ মেগাওয়াটেরও বেশি ঘাটতি তৈরি করবে।
আরও বড় চিত্র হলো, ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০% নবায়নযোগ্য লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন হবে ৩৫ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ সক্ষমতা। এর জন্য লাগবে ৩৫.২ থেকে ৪২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ।
গবেষণায় বলা হয়েছে, দেশের বিভিন্ন নীতি নথিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ধরা হয়েছে। যেমন—মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান: ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% নবায়নযোগ্য।
নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫: ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০% নবায়নযোগ্য।
সমন্বিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মহাপরিকল্পনা (IEPMP): ২০৪০ সালে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির লক্ষ্য ৪০%।
কিন্তু IEPMP-তে ‘পরিচ্ছন্ন জ্বালানি’র সংজ্ঞায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ ও কার্বন ক্যাপচারের মতো অপ্রমাণিত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা প্রকৃত নবায়নযোগ্য রূপান্তরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।
২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত জাতীয় গ্রিডে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ মাত্র ৩.৬%। বিপরীতে, গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ ৪৩.৪% এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ সক্ষমতা বাড়ছে সমানতালে।
অন্যদিকে, সৌর বিদ্যুৎ বর্তমানে ৭০০ মেগাওয়াট হলেও ২০৪০ সালের মধ্যে এটিকে ১৭,২২৯ মেগাওয়াটে নিতে হবে। বায়ু বিদ্যুতের প্রবৃদ্ধি আরও নাটকীয়—৬২ মেগাওয়াট থেকে ১৩,৬২৫ মেগাওয়াটে পৌঁছানোর লক্ষ্য ধরা হয়েছে।
বিনিয়োগ চ্যালেঞ্জ
সিপিডির গবেষণা অনুযায়ী—
২০২৫–২০৩৫ সময়কালে প্রয়োজন হবে প্রায় ২৪.৭ বিলিয়ন ডলার।
এর মধ্যে সৌর বিদ্যুৎ: ১৬.৫ বিলিয়ন ডলার,
বায়ু বিদ্যুৎ: ১২.৬ বিলিয়ন ডলার,
জলবিদ্যুৎ: ৬ বিলিয়ন ডলার,
আমদানি ও অন্যান্য: ৭.৪ বিলিয়ন ডলার।
বাংলাদেশ ইন্ডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিপিএ) সাবেক প্রেসিডেন্ট ইমরান করিম বলেছেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরানো জরুরি। এলওআই দেওয়া হলেও দ্রুত টেন্ডার নিষ্পত্তি না হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ধীর হবে।
জীবাশ্ম বিদ্যুৎকেন্দ্র অবসরের পরিকল্পনা নেই
সিপিডি বলছে, বিদ্যমান জীবাশ্ম বিদ্যুৎকেন্দ্র অবসরের জন্য বাধ্যতামূলক ও সময়সীমাভিত্তিক কোনো কৌশল নেই। এতে অতিরিক্ত সক্ষমতা ও আর্থিক ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিস্তার ব্যাহত করবে।
সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম সতর্ক করে বলেন,“বাংলাদেশ যদি নীতিগত অস্পষ্টতা ও জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা বজায় রাখে, তবে আর্থিক সংকট ও জলবায়ু লক্ষ্যে ব্যর্থতার ঝুঁকি বাড়বে। এখনই স্মার্ট ও ঐক্যবদ্ধ কৌশল গ্রহণ করতে হবে।”
সিপিডির সুপারিশ
১. ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি লক্ষ্য সমন্বিতভাবে সব নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা।
২. ২০৩০ ও ২০৩৫ সালের জন্য স্পষ্ট মাইলফলকভিত্তিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি, যেখানে জীবাশ্ম বিদ্যুৎকেন্দ্র অবসরের সময়সূচি থাকবে।
৩. নেপাল, ভুটান ও ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ও আন্তঃসীমান্ত বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।
৪. বহুজাতিক উন্নয়ন ব্যাংক (ADB, AIIB, বিশ্বব্যাংক) ও জলবায়ু তহবিলের সঙ্গে কৌশলগত সম্পৃক্ত হয়ে স্বল্পসুদে অর্থায়ন নিশ্চিত করা।
৫. গ্রিড অবকাঠামো, বিদ্যুৎ সঞ্চয় প্রযুক্তি, ছাদে সৌরবিদ্যুৎ ও মিনি গ্রিডের মতো বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থা প্রসার করা।
বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভবিষ্যৎ এখনও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে। জীবাশ্ম জ্বালানির সক্ষমতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে না পারলে জলবায়ু অঙ্গীকার ও জ্বালানি নিরাপত্তা দুটোই ঝুঁকিতে পড়বে।